।। ফরীদ আহমেদ রেজা ।।
আমরা বাবাকে আব্বা বলে সম্বোধন করি এবং মাকে বলি আম্মা। আব্বা তাঁর মাকে শুধু মা বলে ডাকতেন, আম্মা ডাকতেন মাই। আমাদের এলাকায় বাবাকে বাবা, বাজান বলারও প্রচলন ছিল। মাকে ছেলেমেয়েরা আম্মা, মা বা মাইজি বলতে শুনেছি। আদি ও আসল শব্দ ‘মা-বাবা’কে কেনো আমরা বাদ দিয়েছি সেটা আমাদের পক্ষে বলা সহজ নয়। মা-বাবা দু জনই হয়তো সেটা পসন্দ করেছেন, অথবা হতে পারে একজন ওপর জনের উপর নিজের পসন্দ চাপিয়ে দিয়েছেন।
আমার আব্বার মতো সুন্দর ও নিরিবিলি মানুষ আমি জীবনে খুব কম দেখেছি। আমাদের গ্রামে বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রামের মতো মাঝে মাঝে দেন-দরবার বা ঝগড়া-বিবাদ হয়। গ্রাম্য বিরোধ কখনো মারামারি পর্যায়েও চলে যায়। আমাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও তা হয়। কিন্তু কোনো ঝগড়া বা বিরোধে আব্বা কখনো অংশ নেননি বা কারো পক্ষ অবলম্বন করেননি। কোথাও ঝগড়া-বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে কেউ কেউ আব্বার কাছে এসে দোয়া চেয়েছেন। কখনো বিবাদমান উভয় পক্ষ এসে দোয়া চেয়েছেন।
একবার আমাদের গোষ্ঠীর সাথে ওপর এক গোষ্ঠীর মারামারির সম্ভাবনা দেখা দেয়। উভয় গ্রুপ দেশি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। হৈ চৈ শুনে আমি তামাশা দেখার জন্য ঘটনাস্থলে চলে যাই। আমাদের গোষ্ঠীর সরদার আছাব দাদা আমাকে দেখে ডেকে নেন এবং বলেন, ‘তুমি এখানে কেনো এসেছো। এক্ষুণি বাড়ি চলে যাও। তোমাদের পরিবারের কেউ ঝগড়ায় আসার দরকার নেই। তোমরা বাড়িতে বসে দোয়া করলেই হবে।’
আব্বার গায়ের রঙ ছিল ইরান বা আরব দেশের লোকদের মতো লালিমা মাখা ফর্সা। একটু গরম লাগলে বা ঘামলে তাঁর মুখ লাল হয়ে যেতো। ধারালো নাসিকা, চওড়া কপাল, ভরাট মুখ। তাঁর গায়ের রঙ বা উচ্চতা আমরা তিন ভাইয়ের কেউ পাইনি। কোনো সমাবেশে গেলে তাঁর উপর সবার চোখ পড়তো। সুনামগঞ্জ, সিলেট, নেত্রকোনা, মোহনগঞ্জ এবং ঢাকায় তাঁর সাথে পায়ে হেঁটে চলাফেরা করা কঠিন ছিল। পদে পদে তাঁকে থামতে হতো মানুষের সালামের জবাব দেয়া ও তাদের সাথে হাত মিলানোর জন্য। দৈহিক গঠন, বেশভূষা ও মুখাবয়বের কারণে প্রথম দর্শনেই তিনি মানুষের শ্রদ্ধা ও ভয়মিশ্রিত ভালোবাসা অর্জন করে নিতেন। দেখতে রাশভারী বা গম্ভীর মনে হলেও তিনি সকল বয়সের মানুষের সাথে সহজেই মিশতে পারতেন।
আমাদের সাথে আব্বার সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বের। আব্বা গল্প করতেন ধীরে ধীরে। কথা বলার সময় সকল কথা পরিস্কার করে বলতেন। পৃথিবীর নানা বিষয়ে তিনি গল্প করতেন। গলার আওয়াজ ছিল ভরাট।
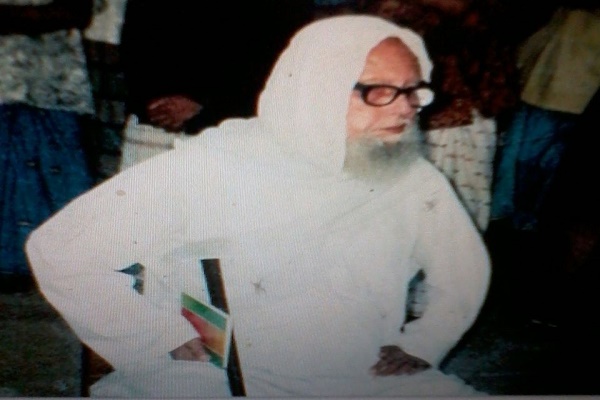
আমরা তাঁর সাথে খেলা করতাম। দাবা খেলায় তিনি ওস্তাদ ছিলেন। বাড়ির গৃহশিক্ষক এবং বড়মামার সাথে তিনি দাবা খেলতেন। আম্মার সাথেও খেলতেন। তাদের খেলা দেখে দেখে আমরাও এক সময় দাবা খেলা শিখে ফেলি। আমরা ভাইবোনের সাথেও আব্বা দাবা খেলেছেন। আব্বা সাপ-লুডু খেলাও খেলতেন। তবে দাবা খেলাই ছিল তাঁর শখের খেলা এবং দাবা খেলায় তিনি কদাচিৎ হারতেন।
একবার আব্বা আমাদের সাথে একটা ভিন্ন রকম খেলা খেলেন। সে সময় আম্মা মামার বাড়িতে নাইওর ছিলেন। আমি আর বড়াপা বাড়িতে আছি। আব্বা এ-৩ সাইজের একটি কাগজ এবং টাকার সাইজে কাটা কিছু মসৃণ কাগজ নিয়ে বসেন। মসৃণ কাগজের টুকরোগুলোকে চাঁদতারা খচিত সিল মেরে হাত দিয়ে কোনো কাগজে পাঁচ টাকা এবং কানোটাতে দশটাকা লেখেন। এ-৩ কাগজে পেন্সিল দিয়ে বেশ কিছু ঘর আঁকেন। তারপর আমরা ভাই-বোনদের ডেকে নিয়ে খেলাটা বুঝিয়ে দেন। নিজ হাতে তৈরি নোটগুলো তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজে রাখেন এবং দু ভাগ আমরা ভাইবোনের হাতে তুলে দেন। কাগজে আঁকা ঘরগুলো দেখিয়ে বলেন, এগুলো আমরা তিন জনের জমি। আমরা খেলার ছলে টাকা দিয়ে জমি ক্রয়-বিক্রয় করবো। সারাদিন আম্মার কথা ভুলে এ নিয়ে আমরা ব্যস্ত সময় কাটালাম। বিকালে আমরা বায়না ধরলাম, মামার বাড়ি যাবো। আব্বা তাতে রাজি হলেন এক শর্তে, আমাদের রাত্রে বাড়িতে চলে আসতে হবে। যদি রাতে বাড়িতে না আসি তা হলে সেদিন যে খেলা শুরু করেছি তা আর হবে না। মামার বাড়ি যাওয়ার পর সমবয়সী মামাদের সাথে খেলায় মেতে বাড়িতে ফিরে আসার কথা ভুলে যাই। রাত্রে মামার বাড়ি রাত কাটিয়ে পরদিন আমরা বাড়িতে আসি। আমি অপেক্ষায় ছিলাম, এক সময় হয়তো আব্বা খেলা শুরু করবেন। কিন্তু সে খেলা আর শুরু হয়নি, সারাদিন আব্বা অন্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটান।
আব্বা তামাক খেতেন। বাড়ির পাশে এক টুকরা জমিতে মস্তান ফুতি তামাক ফলাতেন। সে তামাকেই সারা বছর চলে যেতো। মস্তান ফুতিও তামাক খেতেন। তামাক খাওয়া মানে ধুমপান করা। বাঙালি চা খায় আবার তামাকও খায়, খাওয়াকে এখানে পান করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। তামাক খেতে হুক্কা লাগে, তামাক-টিক্কা ও ছিলিম বা কল্কে লাগে। মস্তান ফুতি নারিকেলের খোল দিয়ে ডাব্বায় তামাক সেবন করতেন। আব্বার ছিল ফর্সি হুক্কা বা বৃন্দাবনী হুক্কা। পিতলের তৈরি হুক্কায় লম্বা নল লাগিয়ে গুড় গুড় করে তামাক সেবন করতেন। একটা কাঠের ট্রে ছিল ছিলিম রাখার জন্য। সকাল বেলা বাড়ির কেউ একজন সেখানে দশ-পনেরোটি ছিলিম সাজিয়ে রাখতো। ছিলিম ছিল মাটির তৈরি। কোনো একজন পিতলের ফর্সি হুক্কা পুকুর ঘাটে নিয়ে ঘষেমেজে চকচকে করে হুক্কায় নতুন পানি ভরে রাখতো। যখনই দরকার পড়তো আব্বা হাঁক দিয়ে বলতেন, কে আছে এখানে, ছিলিমটা বদলে দাও। মাঝে মাঝে আব্বা তামাকের জন্য সুগন্ধি কিনে আনতেন। একটা ছিল খামিরা তামাক। সেটা সেবন করলে পুরো এলাকায় এর সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়তো।
আব্বার আরেকটা এবং বলতে গেলে প্রধান নেশা ছিল বই পড়া। আব্বার কথা মনে হলে প্রথমেই একটা ছবি মনের কোনে ভেসে ওঠে। বাংলা ঘরের বারান্দায় বা পুকুর পাড়ে গাছের তলায় আব্বা ইজি চেয়ারে বসে আছেন। হাতে বই আর পাশে তাঁর পিতলের ফর্সি হুক্কা। ধ্যানমগ্ন হয়ে তিনি সেখানে বসে সকাল থেকে দুপুর বই পড়তেন। দুপুরে গোসল-নামাজ সেরে ও খাবার খেয়ে আবার বই নিয়ে সেখানে চলে যেতেন। কেউ দেখা করতে এলে সেখানে বসেই তার সাথে কথা বলতেন। কাউকে আপ্যায়ন করার প্রয়োজন হলে ডাক দিতেন, ‘ওই কি নাম!’ বাড়ির কেউ ডাক শুনে ছুটে এলে বলতেন একটা চা নিয়ে এসো। চায়ের সাথে সব সময় অন্যকিছু থাকতো। আব্বা চা খেতেন না। অতিথি বিদায় নেয়ার পর আবার বই খুলে পড়া শুরু করতেন। অন্য কোনো কাজ না থাকলে বা সফরে না গেলে এটাই ছিল আব্বার নিয়মিত রুটিন। সফরে গেলেও কয়েকটা বই তাঁর সাথে থাকতো।
আব্বার পছন্দের বই কি ছিল সে প্রশ্নের জবাব দেয়া সহজ নয়। তাঁর নিজের একটা লাইব্রেরী ছিল। এর নাম ছিল শমিসুদ্দীন মেমোরিয়েল লাইব্রেরী। প্রাইমারী স্কুল শেষ করার পর আব্বা লাইব্রেরীর চাবি আমার হতে তুলে দেন। তখন তাঁর সকল বই আমি উল্টেপাল্টে দেখি। সেখানে নানা প্রকারের বই ছিল। ঢাকা ও কোলকাতা থেকে প্রকাশিত গল্প, উপন্যাস, ইসলামী বই, অনুদিত বই, বাঁধাই করা সাহিত্যপত্র, শিশুতোষ বই, ভ্রমণ কাহিনী, ইতিহাস, আত্মকথা, গোয়েন্দা কাহিনী – সবই ছিল সেখানে। আব্দুল হাকিম অনুদিত কুরআনের বাংলা তাফসির ছিল, আরো ছিল কোলকাতা থেকে প্রকাশিত বসুমতি, ভারতবর্ষ, শিশির প্রভৃতি পত্রিকার বাঁধাই করা সেট। নজিবর রহমানের লেখা এক সময়ের সাড়া জাগানো উপন্যাস আনোয়ারা, প্রেমের সমাধি এবং সৈয়দ এমদাদ আলীর লেখা আব্দুল্লাহও সেখানে ছিল। একদিন সাদা কাপড়ে মুড়ে রাখা একটা বই দেখতে পাই। কৌতুহলী হয়ে আমি আব্বাকে কাপড় দিয়ে মুড়ে রাখার কারণ জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, এটা নিষিদ্ধ বই। বইটির নাম ছিল ভাসানী যখন ইউরোপে। কয়েকটি বই ও ম্যাগাজিনে সৈয়দ উসমান আলী সারং-এর নামে সিল মারা রয়েছে। এ ব্যাপারে আব্বাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সৈয়দ ওসমান আলী সারং সৈয়দপুরেরই একজন প্রবীণ বইপ্রেমিক মানুষ। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে অনেক বই ছিল। তিনি গ্রাম ছেড়ে সিলেট শহরে চলে যাওয়ার সময় এ সকল বই ও পুরাতন ম্যাগাজিন আব্বার লাইব্রেরীতে দান করে যান। আব্বার লাইব্রেরীর বই নড়াচড়া করলেও সে সময় এ সকল বই পড়ে বুঝার বয়স আমার ছিল না। আব্বার মুখ থেকেই পারিবারিক আসরে বা ভিন্ন সময় অনেক বইয়ের গল্প শুনে আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।
আমাদের বাড়িতে ডাকযোগে কিছু পত্রপত্রিকা আসতো। এর মধ্যে ছিল ঢাকা থেকে দৈনিক আজাদ ও মাসিক মোহাম্মদী এবং সিলেট থেকে আল ইসলাহ ও যুগভেরী। আব্বা সিলেট কেন্দ্রিয় সাহিত্য সংসদের জীবন সদস্য ছিলেন। সিলেট গেলে সেখান থেকে ১০টি বই এবং দুয়েকটা ম্যাগাজিন নিয়ে আসতেন।
আমার দাদার মতো আব্বাও অনেক মারিফতি গান রচনা করেছেন। অবশ্য তাঁকে আমি কখনো গান গাইতে দেখিনি। বাড়িতে গানের আসর বসলে তিনি সেখানে গিয়ে কখনো কিছু সময়ের জন্য বসতেন। কিন্তু তিনি গায়কদের সাথে সুর মিলিয়ে গান গেয়েছেন, এমনটি আমার নজরে পড়েনি। আমাদের বাড়িতে প্রতি বছর একবার শিরনি বা সিন্নি হতো। এটাকে ওরসও বলা হয়। আব্বা-আম্মা এটা শিরনি বলতেন। এ উপলক্ষে আব্বাও দাদার মুরিদরা আসতেন। সে সময় আম্মা ও আব্বার ব্যস্ততার সীমা থাকতো না। আব্বা এক সময় আমাকেও এ ব্যাপারে একটি দায়িত্ব দেন। আমাকে ডেকে নিয়ে আগত অতিথিদের ছাতা সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করেন। কি ভাবে তা করতে হবে তাও বলে দেন। আমাকে ছোট এক টুকরা কাগজে যার ছাতা তার নাম লেখে আঠা দিয়ে ছাতায় লাগিয়ে রাখতে হবে। দায়িত্বটি পেয়ে আমি খুব উৎসাহের সাথে তা পালন করি।
ওরস নাম শুনলে বাঙালি পাঠকদের মনে যে চিত্র ভেসে ওঠে, আমাদের বাড়ির ওরস ছিল তা থেকে ভিন্ন। ওরসের দিন এশার নামাজের পর গ্রামের একজন বা দুজন আলেম আসতেন। তিনি কিছু ওয়াজ নসিহত করে মিলাদ পড়াতেন। মিলাদে ক্বিয়াম ছিল না। বসে বসেই দুরুদ বা মিলাদ পড়া হতো। দু জন আলেমের কথা আমার মনে আছে যারা ওরসের সময় আমাদের বাড়িতে এসে মিলাদ পড়িয়েছেন। একজন সৈয়দ পুর কওমী মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা এবং হোসেইন আহমদ মাদানীর খলিফা আব্দুল খলিকের সন্তান এবং শায়খে বরুনার খলিফা মাওলানা সৈয়দ আবু সাঈদ। ওপর জনও কওমী মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রউফ। ছাতকের মাওলানা হিসেবেই তিনি পরিচিত ছিলেন। ছাতকের মাওলানা সাহেব এক সময় আমার মামার বাড়িতে থাকতেন। তখন তাঁর কোলে বসে আমি সুরা ফাতিহা মুখস্ত করেছি। ওয়াজ-নসিহতের পর দোয়া হতো। এরপর শুরু হতো দ্বিতীয় পর্ব। দ্বিতীয় পর্বে আব্বা ও দাদার মুরিদরা মারিফতি গান গাইতেন, তাদের ভাষায় সেটা ছিল কালাম। সেখানে গানের সাথে কোনো বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার হতে আমি দেখিনি। এ ব্যাপারে আব্বার কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল। মধ্যরাত্রে মুরিদানের লোকদের সামষ্টিক জিকর দেখার জন্যে আমাদের বাড়িতে গ্রামের অনেকে হাজির হতেন। ফজর পর্যন্ত এ পর্ব চলতো। জামাতের সাথে ফজরের নামাজ পড়ার পর কুরআন খতমে সবাই বসে যেতেন। সেখানেও গ্রামের কিছু হাফিজ এবং আলেম অংশ নিতেন। খতমে কুরআনের পর গরু জবাই করা হতো। কখনো একটা বা দুটো খাসিও জবাই হতো। জোহরের নামাজের পর ভাত ও মাংসের তরকারি দিয়ে তৈরি শিরনি উপস্থিত সবাইকে বিতরণ করা হতো। আমাদের প্রতিবেশী ও ঘনিষ্ট আত্মীয়রা এ সকল কাজে সব সময় আব্বাকে সহযোগিতা করতেন। (চলবে…)

