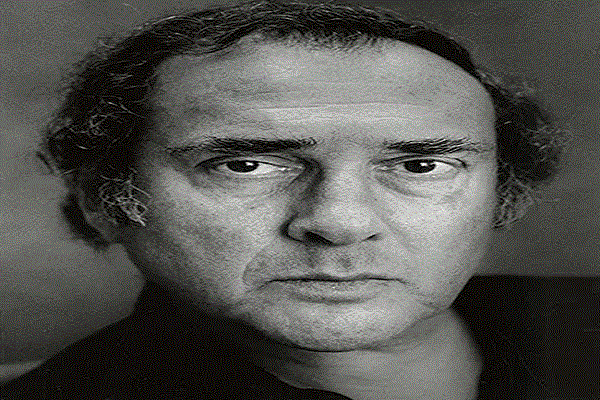।। তর্জমা – হোসেন মোফাজ্জল ।।
হ্যারোল্ড পিনটার লন্ডনে ১৯৩০ জন্মগ্রহণ করেন। বিয়ে করেন আনতোনিয়া ফ্রেজারকে। ১৯৯৫ সালে সাহিত্যে সারাজীবনের অবদানের জন্য ডেভিড কোহেন বৃটিশ সাহিত্য পুরষ্কার পান। ১৯৯৬ সালে নাটকে সারাজীবনের অবদানের জন্য লরেন্স অলিভার পুরষ্কার পান। ২০০২ সালে সাহিত্যে অবদানের জন্য কম্পেনিয়ন অফ অনার পান এবং ২০০৫ সালে কবিতার জন্য উলফ্রেড ওয়েন পুরষ্কার পান। ২০০৫ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরষ্কার পান আর ২০০৭ সালে পান ফরাসী লিজিয়ন দ্য অনার। ২০০৮ সালে লিভার ক্যান্সারে মারা যান। বর্তমান লেখাটি হ্যারোল্ড পিনটার – ভেরিয়াস ভয়েসেস: প্রোজ, পোয়েট্রি, পলিটিক্স ১৯৪৮-২০০৫ থেকে তরজমা করা।)
ইনডেক্স অন সেনসরশিপ, মে ১৯৯২
American Football ( A Reflection upon the Gulf War)
Hallelujah!
It works.
We blew the shit out of them.
We blew the shit right back up their own ass
And out their fucking ears.
It works,
We blew the shit out of them
They suffocated on their own shit!
Hallelujah!
Praise the Lord for all good things.
We blew them into fucking shit.
They are eating it.
Praise the Lord for all good things.
We blew their balls into shards of dust,
Into shards of fucking dust.
We did it.
Now I want you to come over here and kiss me on the mouth*
আমি কবিতাটা লিখতে শুরু করেছিলাম ১৯৯১ এডিনবরা উৎসবে উড়োজাহাজে যাবার পথে। নামার প্রাক্কালেই একটা রাফ ড্রাফট আমি নামিয়ে ফেলেছিলাম। এর শুরুটা হয়েছিল জয়জয়াকার দিয়ে, মারদাঙ্গা, বিজয় প্যারেড, যা কি-না সেই সময়ের সাবুদ হিসেবে তার ভেতর থেকে লাফিয়ে উঠেছিল। যার কারণে লেখা হয়েছিল ‘উই ব্লিউ দ্য শিট আউট অব দেম’। প্রথমে আমি লেখাটা পাঠিয়েছিলাম লন্ডন রিভিয়্যু অব বুকস এ। সেখান থেকে আমি ভয়ানক আজিব একটা উত্তর পেলাম। যা বলা হয়েছিল তার সারাংশটা হচ্ছে, কবিতাটিতে বড়রকমের জোর খাটানো হয়ে্েছ, আর এই কারণেই তারা আমরা কবিতাটি প্রকাশ করতে পারছে না। কিন্তু চিঠিতে অসাধারণভাবে দাবী করা হয় বিশ্বব্যাপী ইউএসএ সর্ম্পকে আমার যা দৃষ্টিভঙ্গি তাদের কাগজ তা শেয়ার করে। আমি ফিরতি ডাকে বললাম ‘পত্রিকাটি আমার দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে, তাই না কি? আরও বললাম ‘আমি যদি তোমাদের জায়গায় হতাম তবে আমি তা আমার ভেতরেই ছুপিয়ে রাখতাম, ইয়ার,’ আমি খুব তৃপ্তি পেয়েছিলাম ‘ইয়ার’ শব্দটা ব্যবহার করে।
তাই আমি লেখাটা পাঠিয়ে দিলাম গার্ডিয়ান এ এবং তারপর সাহিত্য সম্পাদক সাহেব আমাকে ফোন করে বললেন ‘ওহ ডিয়ার।’ তিনি যোগ করেন, ‘হ্যারোল্ড, সত্যটা কী … তুমি এটা দিয়ে সত্যি সত্যি খুব বাজে রকমের মাথা ব্যথার কারণ হয়েছ আমার জন্য ।’ তিনি বলেন, ‘ব্যক্তিগতভাবে বলছি, আমি নিজে পুরোপুরি তোমার পেছনে রয়েছি’, ‘কিন্তু’ তিনি বলেন ‘আমার মনে হয় না তুমি বুঝবে. . . ওহ্ আমার কী মনে হয় জানো? আমরা সত্যিকার অর্থে ঝামেলায় পড়ে যাব যদি এটা গার্ডিয়ানে ছাপানোর চেষ্টা করি।’ সত্যি সত্যি, আমি নির্মলভাবে জিজ্ঞেস করি, এমটা কেন হচ্ছে?
তিনি আমাকে বলেন, ‘বেশ, হ্যারোল্ড, তুমি তো জানো, আমরা একটা পারিবারিক খবরের কাগজ।’ সত্যি সত্যি এই কথাগুলো সে বলেছিল। ‘ওহ, আমি সরি,’ আমি বলেছিলাম ‘আমার তো এমনটাই জানা ছিল তোমরা একটা সিরিয়াস নিউজপেপার।’ তারপর তিনি বলেন, ‘বেশ, হ্যাঁ, আমরা একই সাথে অবশ্যই একটা সিরিয়াস নিউজপেপার। সে যাই হোক, গেল কয়েক বছরে গার্ডিয়ান এর অনেককিছুই খানিকটা বদলেছে।
আমি তাকে বাতালাম সে যেন তার কিছু কলিগের সাথে কথা বলে দিন কয়েক বাদে আমাকে জানায়। কারণ, আমি বললাম, ‘আমি বিশ্বাস করি গার্ডিয়ান এর একটা দায়িত্ব আছে সিরিয়াস লেখা প্রকাশ করার, সিরিয়াস বিবেচিত হয় এমন কাজগুলো, এবং আমি মনে করি এই কাজটাও তাই, যদিও এটা বেশ উত্তপ্ত, একই সাথে আমি মনে করি এটা ইস্পাতিয়। উত্তপ্ত ইস্পাত. . .।’
দিন দুয়েক বাদে তিনি আমাকে ফোন করেন এবং বলেন ‘হ্যারোল্ড, আমি ভয়ানক রকমের সরি, আমি এটা প্রকাশ করতে পারছি না।’ সে মোটামুটি এটাও বললো, এটা তার চাকুরীর থেকেও বেশী দামি। এই হচ্ছে গার্ডিয়ান। আমি এবার লেখাটা পাঠিয়ে দিলাম অবসারভার পত্রিকায়।
অবসারভার হচ্ছে সবচেয়ে জটিল এবং আকর্ষণীয় জাল যার ভিতর দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছিল। আমি কবিতাটি সাহিত্য সম্পাদককে না পাঠিয়ে সরাসরি সম্পাদকের কাছে পাঠিয়েদিলাম।
দিন কয়েক বাদে সম্পাদক সাহেব আমাকে ফোন করে বললেন তিনি মনে করেন কবিতাটি প্রকাশ করা যায়। তার মতে লেখাটায় বেশ পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছে। সম্ভবত এটা নিয়ে বেশ বাকবিতন্ডাও হতে পারে, তিনি বলেন, কিন্তু তার মনে হয় এটা ছাপানো উচিত কিন্তু সাহিত্য পাতায় না বরং ‘লিডার’ পাতায়। এটা সত্যিকার অর্থে একটা রাজনৈতিক কবিতা, তিনি বলেন। আমি তা শুনে বেশ পুলকিত হয়েছিলাম। বললেন তিনি আমাকে একটা প্রুফ পাঠাবেন, তিনি তা করলেনও।
পরের রোববার কিছুই ঘটলো না। এবং তারপরের রোববারও কিছুই ঘটলো না দেখে আমি সম্পাদক সাহেবকে ফোন করলাম। তিনি বলেন ‘ ওহ, ডিয়ার হ্যারোল্ড, আমরা ভয় হচ্ছে তোমার কবিতায় একটা বা দুটো সমস্যা রয়েছে।’ আমি তার কাছে জানতে চাইলাম সেগুলো কী। ‘সংক্ষেপে, আমার কলিগরা চায় না এটা আমি ছাপাই।’ কেন? আমি জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন ‘তারা আমাকে বলেছেন এটা ছাপালে আমরা অনেক পাঠক হারাবো।’ আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কী সত্যি এমনটা বিশ্বাস কর? সে যাই হোক তার সাথে আমার বেশ অনেকক্ষণ ইয়ারসুলভ আলাপ হল। তিনি জানালেন, ‘আমি এটা ছাপাতে চাই কিন্তু বলতে পারো আমি প্রায় একঘরে হয়ে যাব।’ তার উওরে আমি তাকে বললাম- দেখো, অবসারভার একটা সিরিয়াস পত্রিকা, সত্যি করে বললে অতি সাম্প্রতিক ইউএস ট্যাংকগুলো আসলে মরুভূমিতে কী করেছে তার প্রকৃত ঘটনা অবসারভার ছেপেছে। ট্যাংকগুলোতে বুলডোজার ছিল, এবং স্থল হামলার সময় তারা এসবকে ব্যবহার করেছে সুইপার হিসেবে। আমি যদ্দুর জানি, তারা অসংখ্যক ইরাকিকে জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে ফেলেছিল। তোমাদের পত্রিকা প্রকৃত ঘটনা হিসেবে এসব রিপোর্ট করেছে এবং এসব ছিল ভয়ঙ্কর এবং জঘন্য রকমের সত্য। আমার কবিতায় সত্যি সত্যি বলা হয়েছে, ‘দে সাফোকেটেট ইন দেয়ার ওউন সিট।’ এটা জঘন্য জানি, কিন্তু এটা জঘন্য রকমের সত্যকেই নির্দেশ করে।
তিনি বলেন ‘পুরোটাই সঠিক, দেখো, আমি চাই কবিতাটা ছাপাতে, কিন্তু আমি বিভিন্ন রকমের বাধার সম্মুখীন হচ্ছি। ঝামেলাটা পাকিয়েছে ভাষা, এটা অশ্লীল ভাষা। মানুষজন এতে বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছে এবং এই কারণে তারা মনে করেছেন আমরা পাঠক হারাতে যাচ্ছি।’ এরপর আমি অবসারভার এর সম্পাদককে একটা ছোট করে ফ্যাক্স পাঠাই, যেখানে আমি নিজের কথার উদ্ধৃত দিয়ে বলি যখন আমি ১৯৮৫ মার্চে আঙ্কারায় আর্থার মিলারের সাথে ইউএস অ্যাম্বেসিতে গিয়েছিলাম তখন আমরা রাষ্ট্রদূতের সাথে তুরস্কের কারাগারগুলোতে যে অত্যাচার হচ্ছে সেসব নিয়ে আলাপ তুলেছিলাম। রাষ্ট্রদূত আমাকে বলেছিলেন আমি বাস্তব অবস্থাটাকে তারিফ করছি না, পাশাপাশি এই অবস্থার উল্টো দিকে যে কম্যুনিস্ট হুমকি রয়েছে, সেনা বাস্তবতা, কূটনীতিক বাস্তবতা, কৌশলগত বাস্তবতা ইত্যাদি ইত্যাদি রয়েছে তা নিয়ে বলছি না।
আমি তাকে বলেছিলাম আমি যা উল্লেখ করছি তা হল একজনের লিঙ্গে ইলেট্রিক কারেন্ট ঢুকিয়ে দেবার মত বাস্তবতা নিয়ে। ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রদূত আমাকে বলেন, ‘স্যার, আপনি আমার বাড়ির অতিথি,’ এবং এই বলে ঘুরে চলে যান। আমি বাসাটা ছেড়ে বেরিয়ে আসি।
যে ব্যাপারটা আমি অবসারভার এর সম্পাদককে বুঝাতে চেয়েছিলাম তা হল রাষ্ট্রদূত সাহেব বড় ধরনের অপমানিত বোধ করেছিলেন লিঙ্গ শব্দটাতে। কিন্তু পরিস্থিতির বাস্তবতা, সত্যিকারের বাস্তবতা হচ্ছে তোমার লিঙ্গের ভেতর দিয়ে ইলেকট্রিক কারেন্ট ঢুকিয়ে দেয়াটা, যা কি-না তার কাছে কোন ব্যাপারই মনে হল না। এই শব্দ ব্যবহার করাটা অপমানের, কিন্তু কাজটা কিছুই না। আমি তাকে বললাম আমি একটা তুলনামূলক রেখা টানতে চেয়েছি এই সামান্য অদলবদলের মধ্য দিয়ে, এবং আমরা যেটা নিয়ে এখন কথা বলছি। এই কবিতায় যেসব অশ্লীল অশ্রাব্য শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তা আসলে এই অশ্লীল কাজকর্ম আর অশ্লীল মনোভাবকে তুলে ধরার জন্যই।
কিন্তু অবসারভার এর সম্পাদক সাহেব আমাকে অতি দুঃখের সাথে লিখলেন এবং বললেন তিনি তা ছাপাতে পারবেন না।‘আমি’ তোমার গালফ যুদ্ধ নিয়ে লেখা কবিতা ছাপাবার জন্য সিরিয়াসলি ভেবেছি, এবং তুমি জানো, আমার প্রথম প্রলোভনটা ছিল তোমার লেখার পক্ষে, এমনকি আমার সিনিয়র কলিগরা লেখাটা ছাপা হলে অনেক পাঠক ক্ষুব্ধ হতে পারেন এ ব্যাপারে সর্তক করার পরেও. . . আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে আমি শঙ্কিত।’
সাম্প্রতিক অবসারভার এর একজন কলামিস্ট তাদের পত্রিকায় একটি কবিতা প্রত্যাখানের ব্যাপারে লিখেছেন। উল্লেখ করেছেন তার সম্পাদকের উদ্বেগের কথা। কিন্তু কেউ বলেন নাই ‘আমাদের মনে হয় না এই কবিতটি যথেষ্ট ভাল। এটা একটা সফল কাজ না।’ আসলে কেউ বলেন নাই।
তারপর আমি কবিতাটি পাঠিয়েছিলাম ইনডিপেন্ডেন্ট এর সাহিত্য সম্পাদকের কাছে, জানালাম আমি তাদের কাছে কবিতাটা প্রথমে পাঠাই নাই কারণ আমার মনে হয় না ইনডিপেন্ডেন্ট কবিতাটি ছাপাতে পারে। কিন্তু এখন যেহেতু সবাই ফিরিয়ে দিয়েছে, লন্ডন রিভিয়্যু অব বুকস, গার্ডিয়ান এবং অবসারভার, সম্ভবত আমি ইনডিপেন্ডেন্টকে ভুল বুঝেছি! বড় গল্প ছোট করে বলি, সাহিত্য সম্পাদক আমাকে জানালেন তিনি কবিতাটি ছাপাতে চান কিন্তু তিনি মনে করেন পত্রিকার সম্পাদক সাহেবকে তার আগে দেখানো উচিত। সম্পাদক সাহেব লেখাটি বেশ কয়েকদিন ধরে রেখে কোন মন্তব্য না করে কেবল জানালেন ইনডিপেন্ডেন্ট কবিতাটা প্রকাশ করছে না। এবং আমাকে কখনও কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয় নি। নাথিং।
আমি কবিতাটি পাঠিয়েছিলাম নিউ ইর্য়ক রিভিয়্যু অব বুকস এ। সম্পাদক আমাকে কবিতাটি পাঠানোর জন্য উষ্ণ অভিনন্দন জানান, কিন্তু বলেন তিনি শঙ্কিত তারা এটা ছাপাতে পারবেন কি-না তা নিয়ে। তাই আমি আর এর পেছনে তেমন সময় নষ্ট করি নি। আমি শুনেছি বোম (Bomb) নামের একটা ম্যাগাজিন, ওয়েস্ট ভিলেজের বেশ নাম করা একটা প্রকাশনা সংস্থা এটা নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে, এবং বস্তুত তারাই কবিতাটা ছাপিয়েছিল।
শেষমেশ ১৯৯২ এর জানুয়ারিতে কবিতাটি বৃটেনে একটি পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, যার নাম হল সোসালিস্ট, সীমিত আকারের প্রচার সংখ্যায়। কিন্তু জাতীয় পত্রিকার বেলায় যতটুকু বলা যায়, এটা ছাপা হয়েছিল হল্যান্ড, ডাচ দৈনিকগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি পত্রিকা হোন্ডোলস্বলড্ (Handelsblad) এ – কোন রকমের অজ্ঞাত শর্তাবলী ছাড়াই, বরং, সম্পাদক সাহেব এর সাথে একটা প্রবন্ধ জুড়ে দিয়েছিলেন ইংল্যান্ডে এটা কীভাবে খারিজ করা হয়েছিল তা নিয়ে। এবং কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল বুলগেরিয়া, গ্রীস এবং ফিনল্যান্ডে।
*কবিতাটা অনুবাদ করলে বাংলায় তার স্বাদ পাল্টে যেতে পারে এ ভয়ে অনুবাদ করা হলো না।